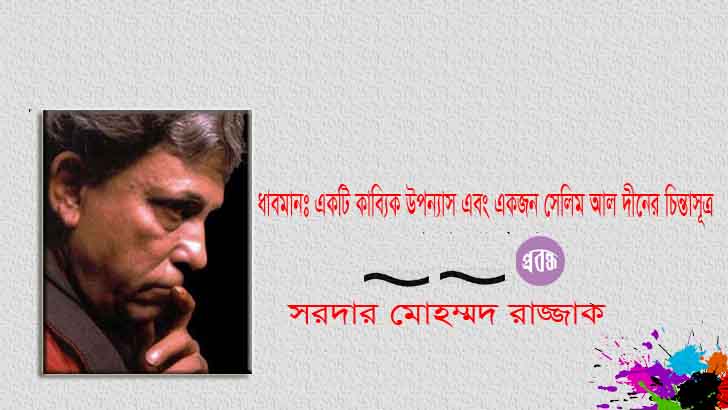
‘অতঃপর হে বুদ্ধ আমি দিক দিগন্তরে মৃত্যুহীন উঠান প্রাঙ্গণে শ্বেত সর্ষপও অন্বেষণ করেছি। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমার প্রাঙ্গণে ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত দেহে- প্রত্যাবর্তনপূর্বক তোমার চরণ প্রান্তে আর্তনাদের ভঙ্গিতে বলেছিলাম।
:আমি শাম্বের গৃহে গিয়ে বলেছি তো তাকে মৃত্যুহীন গৃহ যদি আর যদি থাকে শ্বেত সর্ষপ দাও বাঁচাবো সন্তান।
আমি শাম্বের কুটিরে গিয়ে রোদন করেছি
আছে কিনা শ্বেত সর্ষপ যদি মৃত্যুহীন এ কুটিরে
তবে দাও একমুঠো, বুদ্ধ জীবিত করবেন মৃতবৎস পুনর্বার।
আমি নিঃস্ব, নিষাদ, জয়ন উজ্জয়নের ঘরে গিয়ে
পুনরপি রোদন করেছি।
কিন্তু সবাই বলেছে মৃত্যু এসে পরিজন থেকে
পরিজন নিয়েছে ছিনিয়ে।
হে বুদ্ধ ভগবান।
মৃত্যুহীন গৃহ নাই হায়
শ্বেত সর্ষপও মিলে নাই যদি
কী হবে এবার কী হবে আমার মৃত এ সন্তানের
কীভাবে বাঁচাবে বলো
স্থির গম্ভীর দৃষ্টি আকাশলোকে পূর্ণচন্দ্রের আভা
তোমার অসীম মুখশ্রীর উপর। তুমিই তো বলেছিলে
অমোঘ মৃত্যুর অমোঘ এই কথা
শ্বেত সর্ষপ বলে দিয়েছে তোমাকে
তবু অনর্থ চোখ থেকে
অশ্রু ক্ষরণ।
আমি তো সে- সে কিনা
কান্না থামিয়ে
স্বচ্ছ চোখে দেখেছে সন্ধ্যার
অসীম আকাশ
জেনে গেছে মৃত্যুর অভ্রান্ত বাঘ নখে
ছিঁড়ে ফেলা হবে ত্বক
কঙ্কাল ঘিরে নাচবে অনাদ্য কালের
কালো বাতাসেরা\
শিরীষ বৃক্ষে ফুটন্ত ফুল। বুদ্ধের মুখে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সাঁঝ আলো। সামনে শিশুর মৃতদেহ। ব্যর্থ, ক্লান্ত শষ্য প্রার্থনাকারী। মৃত্যু অমোঘ জেনে শিশুটি কোলে ধীরে ফিরে যায়, সৎকারের সান্ত¦নায়।
উদ্ধৃত অংশটুকুর পুরোটাই সেলিম আল দীন রচিত ‘ ধাবমান’ নামীয় আখ্যান থেকে গৃহীত। ধাবমান রচনাটির শীর্ষভাগে সেলিম আল দীনের পরিচিত পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি নাটকের মহাকবি। তিনি নিয়ত আঙ্গিকের সীমা ভেঙ্গে চেতনা প্রবাহের ভিতর থেকে ভিন্ন চেতন জগতে প্রবেশ করেন। তৈরি করেন রচনা সমুদ্রের মধ্যে অচেনা আর এক রূপময়ী সমুদ্র। ‘ধাবমান’- তারই সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণ। পরিচিতি পর্বেই উল্লেখিত হয়েছে এই আখ্যানটি মানুষের পরিচিত চিন্তার সীমানাকে ডিঙ্গিয়ে ঢুকে পড়েছে প্রাণীদের বিচিত্র জগতে- আদিম অনুভূতি, গতি আর অভাবিত পরিপার্শ্ব চৈতন্য নির্মাণ করেছে একটি নান্দনিক সফল কাহিনী।
কিন্তু এখানে ‘ধাবমান’- কে আমরা আখ্যান হিসেবে বিবেচনা না করে বরং কাব্যিক উপন্যাস হিসেবেই বিবেচনা করবো। এ কারণে যে তার সমগ্র রচনাটি পাঠ করে রচনাটির রচনাভঙ্গি এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে রচনাটিকে কাব্যিক উপন্যাস হিসাবেই বিবেচনা করবো। এ কারণে যে তার সমগ্র রচনাটি পাঠ করে রচনাটির রচনাভঙ্গি এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে রচনাটিকে কাব্যিক উপন্যাস হিসাবেই আখ্যায়িত করাই বেশি যথার্থ মনে হয়েছে। সেলিম আল দীন আমাদের কাছে মূলত একজন সফল নাট্যকার হিসেবেই অধিক মাত্রায় পরিচিত। তার নাটক রচনার অতি প্রাথমিক কালপর্বের নাটক- ‘জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন’- সে সময়েই একটি বৃত্তাবদ্ধ পরিমন্ডলীয় মাত্রাকে চূর্ণ করে তারই ভাষায় ‘ ঊনপঞ্চাশ বায়ু, খুরে বেঁধে’ অব্যাহত ছুটেছে সম্মুখপানে- তারই সৃষ্ট ‘ ধাবমান’ এর আঙ্গিকে ‘ধাবমান’ এর শক্তিকে ধারণ করে ‘ হঠাৎ ফিনিক রক্ত জলের লোহিত দৃষ্টি’- নিয়েই হনন করেছে অজ¯্র উন্মীলিত নেত্রের কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারকে। হঠাৎ ফিনিক রক্তের ঝিলিক যেন ঝলসে দিয়েছে সে নেত্র সমূহের দৃষ্টি সীমাকে। মোহাবিষ্ট হয়ে প্লাবিত করেছে চতুর্পাশ্বস্থ ‘ পরিপার্শ্ব চৈতন্য’- কে।
তারপর থেকে তার ধাবমানতা আর থেমে থাকেনি। অন্ততঃ ‘বনপাংশুল’- পর্যন্ত। বাংলার গ্রামীণ কালচারের অনাদ্যকালীন একটি অংশ- ‘যাত্রার’ অন্তর এবং অন্তরের .............
তিনি ছিলেন তার রচিত আখ্যান- ধাবমানের মতোই ধাবমান- অবশ্যই সম্মুখ পানে। তিনি মিথ গড়েছেন আবার ভেঙেছেনও নিজ হাতেই- আবার গড়েছেন। অর্থাৎ নাটককে তিনি নীরিক্ষার প্রবল ¯্রােতে ভাসিয়েছেন অনায়াসে। নাটক নিয়ে তিনি ‘লবনাম্বুসমাকীর্ণ জীবন ও মৃত্যুর অনন্ত পরপারের দিকে দৃষ্টিপাত’- না করে ‘মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে’ তিনি গবেষণায় আপ্লুত থেকেও পশ্চাদ্ধাবনকারীর দিকে মোটেও তাকাবার সময় ও সুযোগ কোনোটাই পাননি এবং প্রয়োজনও বোধ করেননি। শুধুই ধাবিত হয়েছেন অনন্ত অসীম অন্ধকার ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা ওহভরহরঃব ঈবৎঃধরহঃু কে উদ্ধারের অন্বেষায়। বোধ করি সে যাত্রা পথের কোনো এক বাঁকে রেখে গেলেন তার অনন্ত আলোকবর্ষের সম্মিলিত আলোক রশ্মিধৌত পদক্ষেপের অত্যুজ্জ্বল ছাপচিহ্ন ‘ধাবমান’- নির্মাণের মাধ্যমে।
তিনি শান্তার গৃহে গমন করেছেন, শাম্বের কুটিরে গিয়ে রোদন করেছেন মৃত্যুহীন গৃহ আর শ্বেত সর্ষপ করেছেন এক মুঠো- ‘বুদ্ধ জীবিত করবেন মৃত বৎস পুনর্বার’- বলে। তিনি ‘নিঃস্ব, নিষাদ, জয়ন উজ্জয়নের ঘরে গিয়ে পুনরপি ‘রোদন’- করেছেন। কিন্তু সবাই বলেছে মৃত্যু এসে পরিজন থেকে পরিজন নিয়েছে ছিনিয়ে। তিনি আক্ষেপ করেছেন ‘ হে বুদ্ধ’ ভগবান মৃত্যুহীন গৃহ নাই হায়, শ্বেত সর্ষপও মিলে নাই যদি, কী হবে এবার, কী হবে আমার মৃত এই সন্তানের, কীভাবে বাঁচাবো বল স্থির গম্ভীর কষ্ট আকাশলোক। এর পরেই তিনি তিরস্কার করেছেন ভগবানকে এই বলে যে পূর্ণ চন্দ্রের আভা তোমার অসীম মুখশ্রীর উপর। ভগবানকে তীব্র তিরস্কার করে তিনি অজাত সর্বস্ব এক প্রকার মনুষ্যকুল নামীয় একটি অতি নি¤œ পর্যায়ের...........
এখন এই যে হরিণীর গর্ভ থেকে মাংসপিন্ডের প্রসব এবং সেই মাংসপিন্ডকে তুলোতে জড়িয়ে ফাতেমার উদরে বন্ধন এবং একদিন, দুইদিন করে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর সেই মাংসপিন্ডের দুই চক্ষুর উন্মিলন- অর্থাৎ একটি নবজাতকের সৃষ্টি এবং ‘ মক্কার শহর’ থেকে আগত জনৈক ‘আলীশাহ’ কর্তৃক সে নবজাতকের ‘মাদার মণি’ নামে নামকরণ সেই সাথে হামেলা ও হরিণীয় সামঞ্জস্য দেখে নহবত আলীর অভিভুক্ত হয়ে যাওয়া, হামেলার পুরুষ বাছুর প্রসব এবং বাছুরসহ হামেলার সুস্থজীবন আর বাছুরটির ‘ সোহরাব’ নামকরণের ওপর ‘মাদার বাবা’- এর অনুমোদন প্রাপ্তি- তাও আবার নিতান্তই কোকিল নামের একটি পাখির ডাকের মাধ্যমে- এসব কিছুর ওপর সোজা সরল অন্তঃকরণের মাধ্যমে নহবত আলী কর্তৃক অগাধ বিশ্বাসের সাথে নিজে অন্তরে কোনো প্রকার প্রশ্ন ব্যতীতই ধারণ- সবই যে একটি সমাজ তথা একটি জাতির নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট তা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং গোটা সমাজের সম্মুখে অত্যন্ত উলঙ্গভাবে উন্মোচন করেছেন লেখক একটি ছন্দোবদ্ধ পদ্ধতির গভীরতার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে বিবরণ করে- সে দিকটি অবশ্যই আমাদের জন্য, মানুষের জন্য একটি অতিবড় প্রাপ্তি- শিক্ষার্জনের একটি বিশেষ অতি মূল্যবান উপাদান।
এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর ‘লালসালু’র- বিষয়টি আলোচনায় আপনা আপনি এসে পড়ে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার ‘লালসালু’- উপন্যাসে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সব চাইতে বড় সম্পদ ও সম্বল ধর্মীয় বিশ্বাসকে মৌলিক মূলধন হিসাবে ‘লালসালু’- উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ‘মজিদ’- এর মাধ্যমে গ্রহণ করে সেই বিশ্বাসের ওপর আত্মস্বার্থ সিদ্ধির গর্ভজাত উচ্চাকাক্সক্ষার নিখুঁত প্রলেপ জড়ানোর মাধ্যমে ধর্মীয় কুসংস্কারকে অত্যন্ত উলঙ্গভাবে গোটা সমাজের সম্মুখে অনাবৃত করে ‘মজিদ’ এর লোক ঠকানোর ফতোয়াবাজী ও ভন্ডামীকে উন্মুক্ত করেছেন। কিন্তু শত সহ¯্র মিথ্যাচার আর ভন্ডামির মাধ্যমে সাধারণ দরিদ্র মানুষগুলির বিশ্বাস ‘মজিদ’-এর প্রতি এতটুকুও শিথিল হয় না। এবং মজিদের বাকচাতুর্যে সে বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয়। কিন্তু মজিদ যখন তার প্রথম স্ত্রীর বর্তমানেই দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং সে দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে তুলে আনে- বিপত্তিটি শুরু হয় সেখান থেকেই। মজিদের সকল কর্মকান্ডকেই তার দ্বিতীয় স্ত্রী ‘জামিলা’ ভন্ডামি হিসেবেই আবিষ্কার করে এবং মজিদও তার দ্বিতীয় স্ত্রী কর্তৃক যে ধরা পড়ে গেছে- বিষয়টি টের পেয়ে যায় এবং এ টের পেয়ে যাবার পর থেকে মজিদের আচরণ আরো বেশিমাত্রার হিং¯্রতায় রূপ নেয়। এবং জমিলার উপর তার মানসিক নির্যাতনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সে অজুহাত হিসেবে বেছে নেয় তার আল্লাহর প্রতি ভিত্তিহীনতা, তার কিশোরী সুলভ চপলতা, নামাজ না পড়া এবং স্বামীকে ভয় না করা। সেই সাথে সে প্রচার করে যে, তার উপর জ্বীনের প্রভাব পড়েছে- এই সম্পূর্ণ খোঁড়া যুক্তিকে। মজিদ পুরো ব্যাপারটি চিন্তা করে জমিলাকে যে কোনো মূল্যে তার প্রতি অনুগত থাকার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি বিধানের আবরণে এবং মিথ্যা ফতোয়াবাজীর মাধ্যমে জমিলাকে তার স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবার চরম প্রয়াস গ্রহণ করে। পরিণতিতে জমিলা স্বামীর এই আচরণ লক্ষ করে আরো নিথর হয়ে যায়।
এরই এক পর্যায়ে মজিদ তার নিজের মিথ্যে ধর্মাচারের প্রতি জমিলার আনুগত্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যকুল আশায় নামাজের জায়নামাজে সেজদার ভঙ্গিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন জমিলাকে তার ছোট্ট দু’টি হাতের একটির কব্জি ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে মজিদের অর্থোপার্জনের একমাত্র অবলম্বন তার নিজ স্বার্থে মিথ্যা সৃষ্টি পীর বাবার মাজার ঘরের দিকে। এ অবস্থায় ঘর থেকে উঠোনের মাঝামাঝি এলে জমিলা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে- এবং মজিদের মুখের দিকে তীক্ষè দৃষ্টিতে তাঁকাতে থাকে এবং হঠাৎ মজিদের মুখ লক্ষ্য করে থু-থু বর্ষণ করে। হতবাক হয়ে যায় মজিদ। এ টুকু ছাড়া জমিলা আর কোনো প্রতিবাদ করে না। কিন্তু এতে চরম ক্ষিপ্ত হয়ে মজিদ টেনে নিয়ে যায় জমিলাকে মাজার ঘরে। মজিদের হাতে থাকা দড়ির এক প্রান্ত দিয়ে জমিলার কোমর শক্ত করে বেঁধে অন্য প্রান্ত ঘরের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। ঘরের খুঁটি এবং জমিলার কোমরের মাঝখানে কিছুটা ফাঁক রেখে দেয় মজিদ যাতে জমিলা মাজারের পাশে বসে থাকতে পারে। মজিদ তার ঘরে চলে যায় জমিলাকে আল্লাহ এবং পীর বাবার কাছে মাফ চাইবার নছিহত করে। রাত্রে প্রবল ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টি হয়। ঘর থেকে বের হয় না মজিদ। ঝড় থেমে গেলে প্রত্যুষে মাজার ঘরে প্রবেশ করে মজিদ। জমিলাকে দেখে তার চক্ষু স্থির হয়ে যায়। কিছুটা ভয়ও পেয়ে যায়। লক্ষ্য করেÑ জমিলার মেহেদী দেয়া একটি পা ‘লালসালু’ আবৃত মাজারের গায়ে লেপ্টে দিয়ে ‘হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জমিলা’। পাঁজা কোলা করে ঘরে নিয়ে আসে জমিলাকে মজিদ। বিছানায় শুইয়ে দেয়। এ অবস্থায় জমিলাকে দেখে মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমা চমকে গিয়ে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন করে ‘ মরছে না কি’? এখানেও মজিদ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, বলে- ‘ আরে নাহ্, আছর পড়লে এই রকমটা হয়’। আসলে মিথ্যা ধর্মাচার, মিথ্যার বেসাতির বিরুদ্ধে হাহাকারে ভরপুর জমিলার ছোট্ট হৃদয়টুকু দিয়ে মাজারের গায়ে লাথি মেরে নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে জমিলা। বুঝেছিল শুধু একজন সে নির্বোধ রহিমা। মজিদের প্রথম স্ত্রী। কিন্তু তার করবারও কিছুই ছিল না। নিষ্পাপ কিশোরী জমিলার অতীব মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্যটির চিত্রকল্প আত্মচৈতন্যের নিরিখে অঙ্কন করলে হৃদয়ের রক্ত ক্ষরণে হৃৎপিন্ড আপ্লুত হয়ে যায়। মিথ্যা মোল্লাতন্ত্র কর্তৃক সে তন্ত্রের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মের সত্য বিধানের বিপরীতে ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি শুধু ঘৃণা প্রকাশ অথবা মিন্মিনে প্রতিবাদই শুধু নয়, সার্বিক সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় প্রতিটি মানুষের। পরোক্ষ ভাবে সে ইঙ্গিতই প্রদান করেছেন- ‘ লালসালু’ এর স্বার্থক রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর লালসালু উপন্যাসের মাধ্যমে ধর্মীয় কুসংস্কার, অনাচার অবিচার এসবের প্রতি জমিলার মৃত্যুর মাধ্যমে নিরঙ্কুশ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার আহŸান জানিয়েছেন সমাজের প্রতি। কিন্তু সেলিম আল দীন তার ‘ধাবমান’ কাব্যিক উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার, মিথ্যার সাথে সত্যের তুলনা না করে সত্যের ওপরেই মিথ্যাকে প্রতিস্থাপিত করে এক প্রকার আত্মতুষ্টি লাভ করা সমাজেই ‘ধাবমান’ সোহরাবের মাধ্যমে ভেঙে চৌচির করতে চেয়েছেন অসামান্য রূপে ‘ অবলীলায়’।
‘স্বপ্নাদিষ্ট এসাকের আকস্মিক ‘ আরোগ্য’ সম্ভাবনা- পর্বটির চিত্র সেলিম আল দীন অঙ্কনে ব্রতী হয়েছেন এভাবে- ‘আকাশ প্লাবায়ে আষাঢ় মেঘের দিগন্তে দিগন্তে বাঁটা মেহেদী ফুলের রঙে নীলাঞ্জন হয়ে ওঠে। সোমেশ্বরীর প্রবল গর্জন এবং ঘরের ভিতরে জিয়ানো শোল মাছের উদ্ভাসিত পুচ্ছ সঞ্চালন ঘন বর্ষণ বেগড়ো বাতাস এসাককে বারংবার মোষের বাথানের দিকে টেনে নিয়ে যায়।
নদীর বাণ এসে ঘরদোর ভাসিয়ে নিলে মোষদের গলার দড়ি কেটে দিতে হবে।
সুবতী ধমকে ওঠে : ‘ঘুমাবা, না রাইত ভইরা উচপিচ করবা।’
এরপর ভোরবেলা অনেক কোলাহল, আনন্দ উচ্ছ¡াস, চিৎকার ইত্যাদির মধ্যে নহবতের ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখে এষার কোলে সোনাব্যাঙ আর তাজা কদমফুল। সুবতী এসাককে ধরে কাঁদে আর হাসে আর চুমু খায়। গপ্পি বুড়ি তিন-বান্যার গান গায়। এরই এক ফাঁকে সুবতী চেঁচায়- এসাকের এক পা ভালো হয়ে গেছে। সে এখন ঘরের বেড়া ধরে এক পায়ে হাঁটতে পারে। এই যে এষার কোলে বহন করে আনা সোনা ব্যাঙ আর হাতে কদমফুল, সোমেশ্বরীর প্রবল গর্জন, ঘরের ভেতরে জিয়ানো শোল মাছের পুচ্ছ সঞ্চালন, প্রবল বাতাস কর্তৃক এসাককে বার বার মোষের বাথানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া-এ সবের সাথে এসাকের চধৎধষরংবফ দুটি পায়ের একটির আকস্মিকভাবে ভালো হয়ে যাওয়া এবং এক পায়ে ভর দিয়ে ঘরের বেড়া ধরে হেঁটে চলার কী সম্পর্ক থাকতে পারে- কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ ও প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস ছাড়া।
কেউ যেন স্বপ্নের ভেতর এসহাককে বলছে : “ সোহরাবকে জবাই করলে তার মাংস গ্রামবাসীকে ভোজ দিলে তবেই তর আর একটা পা ভালো হয়ে যাবে। সেই আগুন চোখা জ্বীন। এসহাকের এ কথা শুনে সুবতী কতৃক নহবতকে দশ টাকা দিয়ে গাজী পীরের দরগায় পাঠানো একটা জানের সদকা হিসেবে।
এটা এসহাকের দ্বিতীয় স্বপ্ন দর্শনের বিষয়। যে স্বপ্নে এসহাক নিজেকে দেখে এক পরীর দেশে এবং হঠাৎ সেখানে একটা দুই শিঙ ওয়ালা জীন এসে এসহাককে নির্দেশ করছে সোহরাবকে জবাই করে সোহরাবের জবাইকৃত সোহরাবের রান্না করা মাংস দিয়ে গ্রামের মানুষদেরকে ভোজ দিলে এসহাকের দ্বিতীয় পা টি ভালো হয়ে যাবে। এবং এ স্বপ্ন দর্শনের কথা এসহাক তার বাবা নহবতালীকে না বলে তার মাকে বলে। যে জ্বীনটিকে এসব দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখে সেই জ্বীনটিকেই এসহাক তার দেখা প্রথম স্বপ্নেও দেখেছে।
এসাকের স্বপ্নের বিবরণ শুনে সুবতী আতঁকে উঠে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিলাপ করতে থাকে। বিলাপ শেষে এক পর্যায়ে স্বামী নহবতের প্রশ্নের জবাবে সুবতী বলে- “ নিজের পোলার ভালোই যদি চাও তব্ েসোহরাবের মাইরা পাড়াতে ভোজ দেও”। নহবত চিৎকার করে ওঠে আকাশ ফাটিয়ে- ‘না’।
এরপর সুবতী বাথানে গিয়ে সোহরাবের গলা জড়িয়ে ধরে অবিরাম বিলাপ করতে থাকে-
‘ও বাজান রে
তবে তো আনি নাই বাজান হামেলার মাও যে জন
হামেলারে বিয়ায়ে থুয়ে- নিরুদ্দেশ গেল
তারপর তোর মাওরেও দেইখা-জুড়ায়েছি বুক
বাপের দ্যাশের মইষ। এ কোন বিধির নিদান বাজান
একজন ভালো হবে অন্যের জানের বদলে। আমার একটা পোলা এসহাকের গায়ে জীনের বাতাস লাইগা দুই পা অচল। এ্ক পাও ভালো অইছে আরেক পায়ের দাম চুকায়ে দিতে হয় হপোনের খেলাস।
এইবার কী হবে তর কী হবে বাজান
মরণ দিয়াছে ডাক দিঘল আজান
হারে বিধি
হারে বিধি
এই বিলাপের উত্তর সোহরাব যেন বলে-
মাও গো- এমন কান্দো ক্যান। মরণ জিতার শক্তি আমার আছে তো । মরণ যদি বা আসে শিঙে বিঁধে নিয়ে যাব তারে সোমেশ্বরীর পার কিংবা সে হয় যদি রাজপক্সক্ষী তবে তার চোখ উঠায়ে নিয়ে তাড়াতে তাড়াতে যাব বালুয়া চখে। তারপর চিতাবাঘ যদি আসে দিমু তারে ঠুলির ওপর পাথরের ঠোকা। আমারে ধরবে মরণ এমুন সাহস।
যুবতী আর নহবতালীর বিলাপ আর বেদনায় এসহাকও পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেও আর নিজের পায়ের সুস্থতা ফিরে চায় না। তার পায়ের পরিবর্তে সোহরাব বেঁচে থাকে। বাবা মায়ের কষ্টের লাঘব হোক। কিন্তু তা আর হয় না। গ্রাম জুড়ে রটে যায় সোহরাব এর জীবনের বিনিময়ে এসহাকের দ্বিতীয় পা’টি ভালো হয়ে যাবে এ কারণেই সোহরাবকে জবাই করে গ্রামে ভোজ দেবে নহবত আলী। কষাইরা মোষটি ক্রয় করতে চায়। দাম দর করে। সোহরাবকে হত্যার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।
কিন্তু সবকিছুই বিফল হয়ে যায়। নহবত আলী আর সুবতী একমাত্র পুত্র সন্তান এসহাকের সুস্থ পা-ও আর কামনা করে না।
তারা সোহরাবের জীবনটাকেই এসাকের পায়ের পরিবর্তে বেঁচে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা আল্লাহর নামে সোহরাবকে উৎসর্গ করে। সোহরাবের গলার দড়ি খুলে দেয়। সোহরাব চলে যায়। দূরে- অজানা অনেকদূরে। সোহরাব অদৃশ্য হয়ে যাবার পর নহবত আলী আর সুবতী যেন কিছুটা স্বস্তি ফিরে পায়। তাদের স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে আল্লাহর নামে উৎসর্গীকৃত সোহরাবকে স্বয়ং আল্লাহই রক্ষা করবেন।
এরপর অনেক ঘটনা ঘটে যায়। সোহরাব গেরুয়া গ্রামে প্রবেশ করে তারপর সাধুটিরা আরও পরে মান্দি পল্লীতে সোহরাবকে দেখা যায়। মান্দী পাড়ার নিরীহ লোকজন সোহরাবের জন্য মনের গহনে বেদনা বোধ করে। সোহরাবের দুঃখে সমব্যথী হতে চায়। সোহরাবকেÑ তারা পালিয়ে যেতে হবে। এরই মধ্যে নগদিদের লোকজন আসে সোহরাব এর খোঁজে- তারা সোহরবাকে বধ করবে। কিন্তু তারা সোহরাবকে পায় না।
এরও অনেক আগে ঘটনা ঘটে- এর মধ্যে মন্দিরের বয়োবৃদ্ধ মনীন্দ্র মারাক হঠাৎ করেই একদিন নগদিদের পাড়ায় স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়। অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে খুবই ধীর পায়ে এবং অতিমাত্রায় ক্লান্ত হয়ে। নগদিরা হতবাক এবং আশ্চর্য রকমের ভীত হয়ে পড়ে। মান্দী মনীন্দ্র মারাকের তো নগদিদের পাড়ায় আসবার কথা নয়। কারণ যারা মান্দি স¤প্রদায়ভুক্ত নয় তারাই তো নগদি। এই দুই স¤প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। পার্থক্য থাকলেও উভয় স¤প্রদায়ের মধ্যে একটি বিশেষ কথা- যে কথাটি তাদের মধ্যে প্রবাদের মতো হয়ে গেছে। তাহলো মনীন্দ্র মারাক পিঁপড়া কাক ও মোষের ভাষা বুঝতো। সোমেশ্বরী শীর্ণ হয়ে গেছে। সোমেশ্বরীর বুকে প্রবল জলপ্রপাতের মতো পানির স্রোত আর নেই । অভাব-অভাবের সাীমানা ডিঙিয়ে দুর্ভিক্ষের হৃৎপিন্ডে ঢুকে পড়েছে।
এরকম একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে মান্দিদের এক অতি বয়োবৃদ্ধ এবং বয়সের ভারে ন্যূজ্ব-মনীন্দ্র মারাক নগদিদের গৃহে এসে অন্ন প্রার্থনা করবে- এটা যেন নাগদিদের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নগদিদের বৃদ্ধ মালিক অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে ঠ্ন্ডাায় শুকিয়ে যাওয়া বাসি ভাতের সাথে বাসি খেসারী ডালের সাথে মরিচ পুড়ে ভর্তা করে এনে মনীন্দ্র মারাককে খেতে দেয়। খাওয়া শুরুর পূর্বে মনীন্দ্র মারাক নিজেই কথা বলে।
ঃ পিঁপড়াদের লগে কথা হইছে
ঃ কী কথা হইছে---
ঃ পিঁপড়েরা বইলছে - কাকের ডাক বইলছে এই শাবুন সেই শাবুন না ( অর্থাৎ এই শ্রাবণ সেই শ্রাবণ না)
ঃ আকাশে মেঘের কথা বলছে , গাছের পাতারা বলছে কী হবে, কী হবে , তারপর নদীর অপূর্ণ শাখার তীরের পিঁপড়েরা সার বেঁধে আসছে। পশ্চিম থেকে একদল পিঁপড়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসে পূর্বের দিকে ধাবমান পিঁপড়েদের শুঁড়ে শুঁড়ে লাগিয়ে বলে ঃ কী হবে গো।
ঃ পুবে যাও । পুবে যাও।
ঃ পুবে কেন পশ্চিমেই তো ছিলাম।
ঃ সরে যেতে বলেছে রানীমা।
ঃ ক্যান
ঃ পুবে যাও পুবে।
এখানে মনীন্দ্র মারাকের পিঁপড়ে কাক আর মোষদের ভাষা এবং কথা বোঝার বিষয়টিকে মান্দি এবং নগদি উভয় স¤প্রদায়ই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই বিশ্বাস করে । প্রমাণ হিসাবে তারা উপলব্ধি করতে চায় ভরপুর শ্রাবণ মাস হলেও বৃষ্টির চিহ্ন কোথাও নেই। সোমেশ্বরীর বুকে পানি নেই। সোমেশ্বরী শীর্ণতর-অসুস্থ। সোমেশ্বরীর দু’পারে সবুজের কোনো উচ্ছলতা নেই। চারদিকে শুধু হাহাকার। চিৎকার আর অনাহার। পিঁপড়েদের পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে ধাবিত হওয়ার মধ্যেই যেন এসবের ইঙ্গিত বহন করে। অতএব মনীন্দ্র মারাকের কথাই নির্জলা সত্য। এতে সন্দেহ বা মিথ্যের কোনো অবকাশ নেই। অথচ বাস্তবতার নিরীখে সম্পূর্ণ বিষয়টিই চরম কুসংস্কারের মোড়কে আবৃত। যেহেতু পিঁপড়েদের চলাফেরা কাকদের কা কা ডাক মোষদের চিৎকার ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে শ্রাবণের বৃষ্টি শ্রাবণের প্লাবন জাতীয় বিষয়গুলোর কোনো সম্পর্কই নেই। এবং সোমেশ্বরী নদীটির সৃষ্টির বিষয়টিই একই। সেটি কুস্ংস্কার সেই অন্ধকারাচ্ছন্নতা।
ধাবমান- নামীয় এই কাব্যিক উপন্যাসটির ভেতর যে কয়টি অধ্যায় রয়েছে তার প্রতিটিতেই রচয়িতা যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের অন্ধকারাচ্ছন্নতা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।
‘ধাবমান’ - সোহরাবের মৃত্যুর পূর্ব অবস্থান । সেখানে সোহরাব শ্যামগঞ্জ বাজার পুরোপুরি তছনছ করে দিয়ে পলায়মান অবস্থায় নির্জন পথের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে মেঘমুক্ত আকাশের তারা দেখে মনে মনে বলে : ঐ তারকাপুঞ্জের ভেতরে নেবে যদি নাও, গৃহ ছায়াতলে আছ কিনা প্রভু। পশুর স্বর্গ-নরক কিছুই নেই। --- কেন। তোমাদের বিশাল আকাশের তলে এই শুধু দুটি মাত্র শিংঅলা একটা প্রাণীর বাঁচবার কিছু কি অধিকার নেই। সহসা তার মনে হয় নিস্ফল প্রার্থনার চেয়ে নিজের জন্য নিজের ওপর ঘৃণা অনেক বেশী সান্ত¦না দেবে তাকে।
এখানে এসেই রচয়িতা একটি প্রতিবাদমুখর নিরপরাধ প্রানীর অসহায় এবং করুণ*- মৃত্যুবোধ থেকে উৎসারিত ঘৃণার তী² স্বর দিয়ে তার জন্মকেই ধিক্কার জানায়, তিরস্কার করে। যা প্রকারান্তরে আমাদের মত --- সকল বোধ, বোধাশ্রিত ধারণা ও বিশ্বাসকে তীরবিদ্ধ করে।
অন্তিম ভটিমায় এসে সোরাব আর কোনো প্রকার বিদ্রোহ না করে নিজেই নিজের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই বোধ করি অতি নীরবে নিজের গ্রীবাদেশ বিস্তৃত করে দেয় সমাজের মুখে ঘৃণার থু-থু বর্ষণ করে অন্যায় দিয়ে শানিত ছুরির নিচে। শেষ হয়ে যায় সোহরাব- অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি চাক্ষুস প্রতিবাদ- একটা বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটিয়ে প্রবল অতৃপ্তির ধারক হয়ে।
আর সমগ্র রচনাটি পাঠ করে একথা অনিবার্যভাবে বলা হয় সেলিম আল দীনের কাব্যিক উপন্যাস ধাবমান আমাদের বাংলা সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারে আর একটি নবতর মাত্রার সংযোজন। যে মাত্রা বাংলা সাহিত্যের গতিধারাকে নিরবধি শুধু ‘ধাবমানের’ মতোই ধাবিত করতে থাকবে- অগ্রসরমান নবতর মিথ নির্মিতির দিকে আর সেলিম আল দীন হয়ে থাকবেন উত্তর ধাবিত কালপুরুষ।
